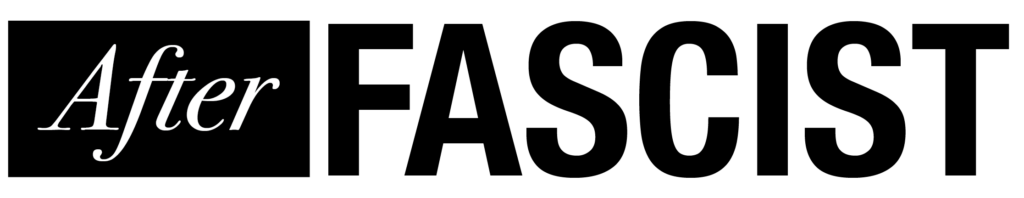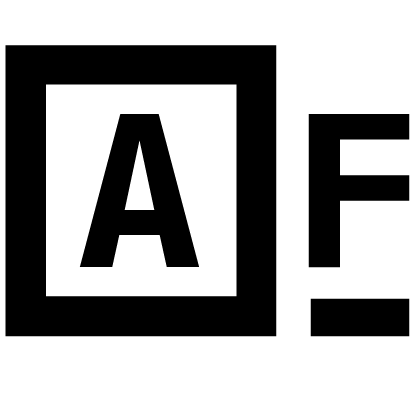কাকে বলে হাসিনা?
হাসিনার পতন কীভাবে হবে, জুলাইয়ের আন্দোলনের আগ পর্যন্ত আমরা অনেকেই এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। আন্তর্জাতিক মোড়লদের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠু নির্বাচন, সরকারের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, হাসিনার মৃত্যু- পতন অনেকভাবেই হতে পারতো। কিন্তু একটা পাতানো নির্বাচনের সাত মাসের মাথায়ই যে অভ্যুত্থানের ফলে এবং গণহত্যার দায় দিয়ে হাসিনাকে এইভাবে পালিয়ে যেতে হবে, এটা অনেকের দূর-কল্পনাতেও ছিলো না। এর কারণ, ফ্যাসিবাদী শাসনের চাকার নিচে পিষ্ট হতে হতে রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে ‘জনগণ’ বাঙলাদেশে হাসি ও করুণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলো। আমরা আমেরিকায় বিশ্বাস রাখলেও জনগণে বিশ্বাস রাখতাম না; জন-অভ্যুত্থানের চেয়ে হাসিনার হার্ট-অ্যাটাকই যেনো আমাদের কাছে বেশি বিশ্বাসযোগ্য সমাধান মনে হতো। বিশেষ করে, বাঙলাদেশের গত পনেরো বছরের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে বেড়ে উঠেছে যে তরুণ সমাজ, তাদের কাছে ‘জনগণ’ একটা ধোঁয়াশার ব্যাপারই ছিলো (অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের বিভাজন এই ধোঁয়াশারই একটা প্রমাণ)। অন্তত এই একটা দিক দিয়ে জুলাইয়ের আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন প্রমাণ করে গেছে যে, রাজনীতির ময়দানে জনগণ আসলে ‘হয়ে ওঠা’র ব্যাপার, কোনো পূর্বপ্রদত্ত ও স্থির ঘটনা নয়৷ আবার এই ‘হয়ে ওঠা জনগণ’ই ভেঙে যেতে পারে বিভিন্ন কারণে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ‘জুলাইয়ের জনগণ’-ও এখন খণ্ডিত, বিভক্ত।
হাসিনার পতনের মতোই অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম হাসিনার শাসনের ধরণ নিয়েও। হাসিনা পরিতাজ্য, সেটা সবাই মানতো। কিন্তু কেনো পরিতাজ্য?- এই প্রশ্নে যথেষ্ট মতভেদ ছিলো। যেমন, ফরাসি ধাঁচের তীব্র সেক্যুলারিজমের পক্ষপাতীদের চোখে হাসিনাকে যথেষ্ট ‘সেক্যুলার’ মনে হয়নি। হাসিনার ‘কওমী জননী’ উপাধিপ্রাপ্তি, হেফাজতের দাবি মেনে বাঙলা পাঠ্যবইয়ে আনীত পরিবর্তন, মদীনা সনদের ভিত্তিতে দেশ চালানোর প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি ঘটনা তারা ভালো চোখে দেখেননি। আবার ইসলামপন্থীরা হাসিনাকে তাজ্য মেনেছেন মূলত তার সরকারের ‘সেক্যুলার ও ইসলামবিদ্বেষী’ চরিত্রের কারণে। শাপলা চত্বরের গণহত্যাসহ মৌলবাদ দমনের নাম করে পশ্চিমা স্টাইলে ইসলাম ও সাধারণ মুসলমান জনগণকে এক ধরনের সাংস্কৃতিক কাঠগড়ায় ঠেলে দেওয়ার জন্য হাসিনা বহুকাল অভিশপ্ত হয়ে থাকবেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সেক্যুলারিজমের হিংসাত্মক ও ফ্যাসিবাদী প্রয়োগের মাধ্যমে জনমানসে ‘সেক্যুলার মানেই ইসলামবিদ্বেষী’ ধরনের সাধারণীকৃত ন্যারেটিভ সৃষ্টির জন্যও দায়ী থাকবেন হাসিনা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। বলাই বাহুল্য, হাসিনা বাঙলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সব্যসাচী শাসক। ডান ও বাম উভয় হাতের ব্যবহারই তিনি এমন নিখুঁতভাবে করেছেন যে, বামের কাছে মাঝেমাঝে মনে হয়েছে তিনি ডান, আবার ডানের কাছে প্রায়ই মনে হয়েছে তিনি বাম। এই আশ্চর্য ধুরন্ধর কালচারাল পলিটিক্স ছাড়া এই রেজিম কি আদৌ পনেরো বছর টিকে থাকতে পারতো?
আবার অনেকেই হাসিনাকে বুঝেছেন মূলত লুটপাটের কাণ্ডারী হিসেবে। হাসিনার কালচারাল পলিটিক্সের চেয়ে হাসিনার লুটপাটকেই তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকেই ‘ফ্যাসিবাদী’ শব্দটা হরেদরে ব্যবহার করতে চাননি, বরং ক্লেপ্টোক্রেসি, পার্সোনালিস্টিক অটোক্রেসি, অথোরিটারিয়ানিজম, কিংবা হাইব্রিড রেজিমের মতো বিদ্যায়তনিক পরিভাষার সাহায্যে বিগত রেজিমকে বুঝতে চেয়েছেন। আমরা যেহেতু বইয়ের পাতার সংজ্ঞার সাথে বাস্তবতাকে মিলিয়ে নিয়ে অগ্রসর হওয়ায় অভ্যস্ত, সেহেতু হাসিনা কিংবা হাসিনাতন্ত্রের বহু বিষয় এখনো ধাঁধা হয়েই রয়ে গেছে । এই ধাঁধাগুলোর আশু সমাধান প্রয়োজন। কারণ হাসিনাকে আমরা কে কেনো প্রত্যাখ্যান করেছি, তার উপরেই নির্ভর করছে আমরা কে কেমন বাঙলাদেশ চাই। আমাদের অতীতের ধারণায় অস্বচ্ছতা থাকলে ভবিষ্যতের ধারণায়ও অনিবার্যভাবেই অস্বচ্ছতা চলে আসবে।
বাস্তবতা হলো, হাসিনাকে কোনো একক সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখা করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে ‘জনগণ’-কে বিলীন ও বিভক্ত করে দেওয়ার জন্য হাসিনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধাঁচের রাজনীতি করেছেন, প্রয়োজন মিটে গেলে সেই রাজনীতিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন হিমাগারে। সুতরাং হাসিনা কী, হাসিনার অর্থ কী, এসব প্রশ্নে জারি থাকা মতবিরোধের একটা বড়ো অংশই মিটে যাবে, যদি আমরা হাসিনার এই বহুচারিতার কথাটা মাথায় রাখি। যাই হোক, আমি নিজে হাসিনাতন্ত্র বলতে বুঝি ‘টোটালিটারিয়ান ক্লেপ্টোক্রেসি’ ধরনের কিছু একটা। রাষ্ট্রের একদম শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত জনগণের সম্পদ লুটপাট আর রাজনৈতিক নিপীড়নের জন্য যে বিশাল সামাজিক-রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক কাঠামো হাসিনা গড়ে তুলেছিলেন, তাকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো টার্ম আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ এই কাঠামোটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই হাসিনা পুলিশ নামক এক ক্যানিবাল দানব তৈরী করেছিলেন। এক ভয়াবহ ও ফ্যাসিবাদী আইনি কাঠামো তৈরী করেছিলেন গণ-মানুষের রক্ত হালাল করার জন্য। এই কাঠামোটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই গত পনেরো বছরে হাজার হাজার মানুষকে গুম-খুন-অপহরণ করা হয়েছে। এবং জনগণের চোখ এই কাঠামো থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই শাহবাগ/শাপলা বিভাজন তৈরী করা হয়েছিলো খুব সচেতনভাবে। বোঝাই যায়, দ্বিতীয় বাকশাল কায়েম না করে হাসিনার আসলে কোনো উপায় ছিলো না। কারণ ন্যূনতম গণতন্ত্রের ধার ধারলে তো এই লুটপাট আর নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। মানুষের সিভিল লিবার্টি নিশ্চিত করতে গেলে তো দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পাচার করা সম্ভব হতো না। তাই দেখা যায়, হাসিনার আমলে মানুষের জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র বাকি রাখা হয়নি, যেখানে রাষ্ট্রের নজরদারি ছিলো না। রাষ্ট্র আর সমাজের মধ্যকার বাউন্ডারি ধুয়েমুছে একাকার করে ফেলা হয়েছিলো পনেরো বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টায়৷ এখন হাসিনা সশরীরে দেশে না থাকলেও ওই সর্বাত্মক রাষ্ট্র রয়েই গেছে। যে সাংবিধানিক কাঠামো দিয়ে এই সর্বাত্মক রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছিলো, সেই সাংবিধানিক কাঠামোও এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও এই সংবিধানের অধীনেই শপথ নিয়েছে। ফলে হাসিনার পালিয়ে যাওয়া যতোটা সত্যি, ঠিক ততোটাই সত্যি প্রায় সর্বশক্তি নিয়েই হাসিনাতন্ত্রের এখনো বহাল থেকে যাওয়া। এই সত্যি আমরা যতো অবহেলা করবো, আমাদের বিপদ ততো বাড়বে।
কোয়ালিটেটিভ টোটালিটি
রাষ্ট্রের এই সর্বাত্মক (total) হয়ে ওঠার ঘটনাটা একদিনে ঘটেনি। গত পাঁচ দশকে বাঙলাদেশে যারা শাসনক্ষমতায় এসেছেন, তাদের সবারই কমবেশি অবদান আছে রাষ্ট্রের এই সর্বাত্মক হয়ে ওঠার পেছনে। এক সরকারের তৈরী করে যাওয়া প্রতিষ্ঠান (যেমন, র্যাব) ব্যবহার করে আরেক সরকার নিজের ও রাষ্ট্রের হাত শক্তিশালী করেছে। এক সরকারের বানানো ড্রাকোনিয়ান আইন বাতিল করার বদলে সেই আইনের পুরোপুরি সুবিধা নিয়েছে পরবর্তী সরকারগুলো। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বময়তা যদি বাঙলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত অবদানই হয়ে থাকে, তাহলে হাসিনার রেজিমের বিশেষত্ব কী?
এইখানে আমরা কার্ল স্মিটের শরণাপন্ন হতে পারি। ১৯৩২ সালে জার্মানির ব্যবসায়ী নেতাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ‘Strong State and Sound Economy’ শীর্ষক এক বক্তৃতায় স্মিট রাষ্ট্রের সর্বাত্মকতা, তথা টোটালিটিকে দুই ভাগে ভাগ করেন। এক. কোয়ান্টিটেটিভ টোটালিটি। এইটার দ্বারা স্মিট বুঝিয়েছিলেন এমন এক রাষ্ট্রকে, যে রাষ্ট্র সর্বাত্মক ঠিকই, কিন্তু সেই সর্বাত্মকতা পরিমাণগত। অর্থাৎ, এই রাষ্ট্রে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেরই রাজনীতিকরণ ঘটে, এবং সেই রাজনীতিকরণের পরিমাণ বা ব্যপ্তির উপর ভর করেই রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সংকটকালীন সময়ে যেকোনো সামাজিক সম্পর্কই আবশ্যিকভাবেই রাজনৈতিক সম্পর্কে পরিণত হয়। মজার বিষয় হলো, স্মিট দেখাচ্ছেন যে এমনকি লিবারেল ডেমোক্রেটিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও রাষ্ট্র এই ধরনের টোটালিটি অর্জন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো নামকাওয়াস্তে ক্রিয়াশীল থাকে ঠিকই, কিন্তু মূল ক্ষমতার চর্চা করে রাষ্ট্র।
সর্বাত্মক রাজনীতিকরণই এখানে রাষ্ট্রের শক্তির উৎস, কিন্তু স্মিট বলছেন, এটা একই সঙ্গে রাষ্ট্রের দুর্বলতাও বটে। কারণ এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজস্ব শক্তির বলে বলীয়ান হতে পারছে না, বরং তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে সামাজিক জীবনে রাজনীতিকরণের ব্যাপকতার উপর৷ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো বলবৎ থাকলে রাষ্ট্রের এই শক্তি বারংবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়, কেননা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সেখানে সর্বদা ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে, এবং রাষ্ট্রকে তারা কখনোই ততোটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে দেয় না, যতোটা শক্তিশালী হলে রাষ্ট্র তাদের অস্তিত্বকেই বিলীন করে দিতে পারে। অর্থাৎ, নিজেদের স্বার্থেই তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সর্বময় হয়ে উঠতে দেয় না। এমতাবস্থায় স্মিট অন্য এক ধরনের সর্বাত্মক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করছেন, যে রাষ্ট্রের টোটালিটি পরিমাণগত নয়, বরং গুণগত। একবার এই কোয়ালিটেটিভ টোটালিটি অর্জন করতে পারলে কোনো রাষ্ট্র তার শত্রুকে কোনো অবস্থাতেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেয় না। কারণ রাষ্ট্র এক্ষেত্রে নিজেই নিজের শত্রু/মিত্র নির্ধারণ করে নেওয়ার ক্ষমতা লাভ করে ফেলেছে। এমনকি জরুরী অবস্থা নির্ধারণের বৈধ ক্ষমতাও রাষ্ট্রের আছে। সুতরাং শত্রুদমনের প্রশ্ন উঠলে রাষ্ট্র তখন গণতন্ত্র কিংবা আইনের শাসনের তোয়াক্কা আদৌ করে না। ভিন্নমত দমন সহজ হয়ে যায় বহু গুণে। তবে এর জন্য রাষ্ট্রের দরকার হয় একটি ফ্যাসিবাদী আইনি কাঠামো এবং একটি শক্তিশালী, গণবিচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্র (সামরিক ও বেসামরিক উভয়ই)। একবার এই দু’টো জিনিস পেয়ে গেলে রাষ্ট্র আর কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল থাকে না। সর্বক্ষেত্রে রাজনীতিকরণও তখন আর আবশ্যক হয় না। কারণ আত্মরক্ষা কিংবা স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব হাতিয়ারই রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে তখন মজুত আছে। দুই ধরনের টোটালিটিই জনগণের শত্রু হলেও কোয়ালিটেটিভ টোটালিটি অপেক্ষাকৃত বেশি ভয়ানক, কেননা এইখানে রাজনৈতিক বর্গ হিসেবে জনগণ একদমই নাই হয়ে যায়।
বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে একটু খেয়াল করে তাকালেই একটা জিনিস সবার চোখে পড়ার কথা। স্মিট যাকে রাষ্ট্রের ‘কোয়ান্টিটেটিভ টোটালিটি’ বলছেন, তা ২০০৯ সালে হাসিনা ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই রাষ্ট্র-কাঠামোয় হাজির ছিলো। এটা বোঝার জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষক হওয়ার প্রয়োজন হয় না। স্মিট যেমন হিটলার-পূর্ব জার্মানিতে লিবারেল ডেমোক্রেটিক কাঠামোর মধ্যেই রাষ্ট্রের কোয়ানটিটেটিভ টোটালিটির অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি বাঙলাদেশেও স্বাধীনতার পর থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর ভেতরেই আমরা রাষ্ট্রের ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার ব্যাপারটা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবো। আমাদের জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক রাজনীতিকরণও দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা একটা ঘটনা। কিন্তু হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর বাঙলাদেশ রাষ্ট্রকে আস্তে আস্তে কোয়ালিটেটিভ টোটালিটির দিকে নিয়ে গেছেন খুব কৌশলীভাবে। আগে থেকেই ভঙ্গুর হয়ে থাকা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি কার্যত রাষ্ট্রের দাসানুদাসে পরিণত করে গণতন্ত্রের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখার ফুরসত এখানে নেই। তবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ভিন্নমত দমন, পুলিশ ও র্যাব নামক ভয়ানক দানব সৃষ্টি, ব্যাপক রাজনৈতিক নিপীড়ন, আয়নাঘর, ভোট চুরি, চব্বিশের গণহত্যা, এক ধরনের ‘স্থায়ী জরুরী অবস্থা’ জারি রেখে দেশব্যাপী ভয়ের রাজ্য কায়েম করা, অসাম্প্রদায়িকতা/ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা/ বাঙালি সংস্কৃতি/ ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি শব্দগুলোতে এক ধরনের ধর্মীয় দ্যোতনা আরোপ করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সাংস্কৃতিকভাবে হীন সাব্যস্ত করা, ইত্যাদি- এই বহুল-চর্চিত ব্যাপারগুলো স্মিটের চিন্তার আলোকে বিবেচনা করে দেখলে আমরা হাসিনার রেজিমের সঙ্গে অন্যান্য রেজিমের পার্থক্যের জায়গাগুলো আন্দাজ করতে পারবো। কোন কোন বিপদের আশু মোকাবেলা না করলে হাসিনা বা আওয়ামীলীগের অনুপস্থিতিতেও বাঙলাদেশে আবারও বাকশাল কায়েম হতে পারে, তারও হদিস পাবো এখান থেকেই।
বাহাত্তরের সংবিধান: ফ্যাসিবাদের ইনকিউবেটর
ফ্যাসিবাদী আইনি কাঠামো এবং শক্তিশালী, গণবিচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্র- এই দু’টো জিনিস না থাকলে হাসিনাতন্ত্রের এতো বাড়বাড়ন্ত আমাদের হয়তো দেখা লাগতো না। আজ আমরা যদি নতুন বাঙলাদেশ গড়তে চাই, তো অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই দু’টি বিপদেরও মূলোৎপাটন করা লাগবে। সেই কাজটা সহজ নয়, কারণ অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বহির্বিশ্বে তো বটেই, এমনকি বাঙলাদেশের ভেতরেও জুলাইয়ের জনগণের শত্রু এবং আওয়ামী লীগের বন্ধুর কোনো অভাব নেই। মুখে যাই বলুক, যেকোনো মৌলিক পরিবর্তনকেই ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রকাঠামোর সুবিধাভোগীরা এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। তাদের উপস্থিতি মেনে নিয়েই আমাদের এই কঠিন কাজে হাত দিতে হবে।
প্রথমেই আসে নতুন সংবিধান রচনার ব্যাপারটা। এখনো অনেকেই বলছেন, নতুন সংবিধান রচনার আদৌ কোনো দরকার নেই, বাহাত্তরের সংবিধানকে প্রয়োজনমতো সংশোধন করে নিলেই চলবে৷ সংবিধান সংশোধন করা বাঙলাদেশে আসলে কঠিন কিছু না। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, তখন সেই সরকার তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সংবিধানকে নিজের মতো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেয়। এর একটা ফল হয়েছে এই যে, আমাদের সংবিধান হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্তরোত্তর রাজনৈতিক কলাকৌশলের একটা বিরাট সংকলন। এইখানে গণ-আকাঙ্খা কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের চুক্তির কোনো হদিস পাওয়া যায় না বললেই চলে। বরং যে গণবিচ্ছিন্ন, ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার জন্য আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো এক প্রকার লালায়িত হয়ে থাকে, সেই ক্ষমতাকেই সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছে বর্তমান সংবিধান। এই সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে বানায় একনায়ক, রাষ্ট্রপতিকে বানায় পুতুল আর সংসদকে বানিয়ে রাখে পঙ্গু। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দোহাই দিয়ে ফ্লোর ক্রসিং নিষিদ্ধ করা হয় আর্টিকেল ৭০-এ। এ এমন এক বন্দোবস্ত, যেখানে সদিচ্ছা থাকলেও সরকার-দলীয় কোনো এমপি কোনো গণবিরোধী সরকারি বিলের বিরুদ্ধে সংসদে ভোট দিতে পারেন না, কেননা নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলেই তার সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। বাহাত্তরের আদি সংবিধানেই এই বিধান ছিলো (শেখ মুজিব নিজে এই বিধানের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন)। এরপর সংবিধানে অনেক রদবদল হয়েছে, প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসির দীর্ঘ পর্ব শেষে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু ফ্লোর ক্রসিং-কে কখনোই অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বারবার সুযোগ পাওয়ার পরও যখন এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় এতো বড়ো ঘাপলা থেকে যায়, তখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাবের নালিশটা আমলে না নিয়ে পারা যায় না।
বর্তমান সংবিধানের আওতায় শুধু যে প্রতিষ্ঠানগুলোই অনিরাপদ, তা নয়। প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশি বিপদে আছি আমরা নাগরিকেরা। এই বিপদের মাত্রাটা বোঝার জন্য মৌলিক অধিকারের নামে প্রচলিত সাংবিধানিক ঘাপলাগুলো একটু বিবেচনা করে দেখা দরকার। ‘গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা’ নামক একটি বইয়ে আলোচকরা দেখিয়েছেন যে, বাহাত্তরের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যে ১৮ টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ১৫ টিই আইনের হাতে বন্দী৷ রাষ্ট্র চাইলে আইনের দোহাই দিয়ে আপনার-আমার অধিকাংশ মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে পারে। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের কথা বলে পুলিশ আপনাকে যেকোনো সময় গ্রেফতার করে আটক করে রাখতে পারে। আবার শত শত মানুষ খুন করলেও সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে রাষ্ট্র পুলিশ বা র্যাবকে দায়মুক্তি দিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ আপনাকে হয়রানি বা হত্যা করার জন্য রাষ্ট্রকে বেআইনি কিছু করতে হয় না, আইনের ভেতরে থেকেই সে আপনাকে যা খুশি করতে পারে। আমাদের সংবিধান, তথা গোটা আইনি ব্যবস্থাই হচ্ছে এমন এক কাকতাড়ুয়া, যে কিনা কাকের কথায় ওঠে আর বসে। যাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আইনের দরকার হয়, তারাই বাঙলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে বাঙলাদেশে পুরোপুরি ‘আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠা হলেও সেটা খুব একটা কাজের কিছু হবে না, কারণ স্বয়ং আইনই তো গণবিরোধী। আইনের ফাঁকফোকরগুলোও কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং সাজানো ও সুপরিকল্পিত।
এই কারণেই নতুন সংবিধান দরকার। সংবিধান হতে হবে এমন, যাতে রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের শাসকেরা সংবিধানের ‘সাংবিধানিকতা’-কে জনগণের বিপক্ষে ব্যবহার করতে না পারে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার রক্ষার নামে যেনো স্বৈরাচারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার সুযোগ না থাকে। সংবিধান হতে হবে এমন, যাতে সংবিধানকে পুঁজি করেই সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রের অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। এই সুযোগ আমাদের দেশে প্রায় নেই বললে চলে। অনেক দার্শনিকই বলেছেন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মোকাবেলায় সহিংস প্রতিরোধের চেয়ে অহিংস, আইনি প্রতিরোধই শ্রেয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বাঙলাদেশে অহিংস হওয়াটা কঠিন না হলেও আইন মেনে আইনি লড়াই চালিয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা বাঙলাদেশে খুব বিরল ঘটনা। আইন মেনেই যে দেশে মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়, সেই দেশে প্রতিবাদের ‘লিগ্যালিটি’ বজায় রেখে ডিসিডেন্ট হওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। আইনই যেখানে হন্তারক, সেইখানে আইনের আশ্রয় চেয়ে কী লাভ? প্লেটোর রিপাবলিকে Ring of Gyges নামে একটা বিখ্যাত অ্যালেগরি আছে। সেইখানে এক রাখাল এমন একটা আংটি খুঁজে পায়, যে আংটি পরলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায় এবং যা খুশি তা-ই করা যায়। ওই রাখাল শেষ পর্যন্ত তার অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে রাজাকে হত্যা করে রাজ্যক্ষমতা দখল করে নেয়। বাঙলাদেশের আইন কিংবা সংবিধানকেও মাঝেমাঝে একটা Ring of Gyges মনে হয়। কারণ এইখানেও আইনের আংটি পরা মাত্র রাষ্ট্র অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু নেপথ্যে থেকে ঠিকই সম্ভাব্য সবরকম নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকে। নিপীড়ন চালানোর জন্য রাষ্ট্রের সবসময় মাঠে হাজির থাকা লাগে না, আইনকানুনই রাষ্ট্রের পক্ষে প্রক্সি দিতে থাকে। এর পরিণতি হয় এই যে, রাষ্ট্র কোনো অপরাধ করলে আমরা সেখানে হয় রাষ্ট্রের উপস্থিতি টের পাই না, নয়তো আইনের উপস্থিতি টের পাই না।
নতুন সংবিধান রচনার মাধ্যমে এইসব জুয়াচুরি থেকে বাঁচার প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার। উল্লেখ্য যে, বাহাত্তরের সংবিধানের গোঁড়ায়ই গলদ ছিলো। ওই সংবিধান যারা রচনা করেছিলেন, তারা কেউই স্বাধীন দেশে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংবিধান লিখতে বসেননি। পাকিস্তানের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে আয়োজিত সত্তরের নির্বাচন থেকেই তারা সংবিধান রচনার লেজিটিমেসি জোগাড় করেছিলেন। এখন পরিস্থিতি আলাদা। বর্তমানে বাঙলাদেশের জনগণই চাইছে নতুন করে সংবিধান রচনা করা হোক। জনগণের চাওয়া-পাওয়াকে সংবিধানে কিভাবে তুলে আনা যাবে, সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে চারিদিকে। শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা মুশকিল, তবে একটা নতুন সংবিধানের প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। আরো আশা করবো, রাষ্ট্রের সর্বাত্মক হয়ে ওঠাকে ঠেকানোর জন্য যা কিছু করা দরকার, নতুন সংবিধানের প্রণেতারা তা করবেন।
সংঘাত ও অনুতাপ
হাসিনার কালচারাল পলিটিক্সের পতন হয়েছিলো সম্ভবত চৌদ্দ জুলাই রাতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার’ স্লোগানের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের প্রথম পতন ওইটাই। আমাদের একটা বড়ো সৌভাগ্য এই যে, জুলাইয়ের দিনগুলোতে আমরা শাহবাগ/শাপলা বিভাজন নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাইনি। ফলে অন্তত ওই কুড়িটা দিন আমরা একতাবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু ছত্রিশে জুলাইয়ের পরে দেখা গেলো শাহবাগ/শাপলা, সেক্যুলার/ইসলাম বিভাজনটা আবারও ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে জুলাইয়ের আন্দোলনের একক ন্যারেটিভ খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে, অন্য পক্ষকে খারিজ করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার’ স্লোগান নিয়েও তুমুল বিতর্ক হয়েছে। অথচ জুলাইয়ের আন্দোলন কোনো একক পক্ষের একক ন্যারেটিভের উপর স্থাপিত কোনো আন্দোলন না। এইখানে ডান, বাম, মধ্য সকলেরই অংশীদারিত্ব ছিলো, এবং এই আন্দোলনের মাহাত্ম্যের জায়গাও এটাই। কোনো একক স্লোগানের আন্দোলনও এটা না। ঢাকা শহরের দেয়ালে আপনি ‘হাসিনা *দি’ এবং ‘হাসিনা *দি না’ উভয়ই দেখতে পাবেন। ‘পুলিশ আমার শাউয়া’ স্লোগানের সাথেই ‘পুলিশ কোন শাউয়া’ স্লোগানও আমরা শুনেছি সমান তালে। এই স্লোগানগুলো আপাতদৃষ্টিতে পরষ্পরবিরোধী, কিন্তু এগুলোর লক্ষ্য ছিলো একটাই: খুনী হাসিনার পতন। একই কথা প্রযোজ্য ‘রাজাকার’ স্লোগানের ক্ষেত্রেও। হাসিনাশাহীর বিরুদ্ধে কথা বললে যদি হাসিনার চোখে রাজাকার হতে হয়, তো আমাদের রাজাকার হতে সমস্যা নেই। ‘তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার’ স্লোগানের জন্ম এই বোধ থেকেই। কিন্তু চৌদ্দই জুলাই রাতে স্টুডেন্টরা এটাও ভুলে যায়নি যে দেশের সবচেয়ে বড়ো গাদ্দার হাসিনা নিজেই, তাই হাসিনার চেয়ে বড়ো রাজাকার আসলে আর হয় না। ফলে ওই রাতেই হাসিনার উদ্দেশ্যে ‘তুই রাজাকার, তুই রাজাকার’ স্লোগানও শোনা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এই ব্যাপারগুলো সবারই কমবেশি জানা থাকা সত্ত্বেও রাজাকার স্লোগান নিয়ে শাহবাগ বনাম শাপলা টাইপের একটা গণ্ডগোল তৈরী হলো। একাত্তরের মুখোমুখি দাঁড় করানো হলো চব্বিশকে। আওয়ামী লীগ ছাড়া এসব ঘটনা থেকে আর কেউ লাভবান হয়েছে কি? এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম কিংবা সেক্যুলারিজমের প্রশ্নে মতভেদ থাকবে, বিতর্ক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বিতর্ক থাকাই উচিত। বহু ধর্ম ও বহু মতের দেশে সুস্থ বিতর্ক না থাকাই বরং আশঙ্কাজনক একটা ব্যাপার। ফলে শাহবাগ আর শাপলাকে সাংস্কৃতিক বর্গ হিসেবে একাকার করে দেওয়ার কথা আমি বলছি না। কিন্তু বিতর্ক যখন হয়ে ওঠে অন্য পক্ষকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করার হাতিয়ার, এবং একটা ন্যারেটিভকে খারিজ করতে গিয়ে যখন একটা পুরো জনগোষ্ঠীকেই খারিজ করে দেওয়ার প্রবণতা তৈরী হয়ে যায়, তখন সেটা বিতর্কের পর্যায়ে থাকে না। বরং বিতর্কের মোড়কে এক ধরনের সহিংস, খারেজী রাজনীতিই প্রাধান্য লাভ করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে। এই খারেজী রাজনীতি তো হাসিনারই সম্প্রসারণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, হাসিনার উন্নয়নের ফাঁকিটা বুঝলেও হাসিনার দুধকলা খেয়েই বেড়ে ওঠা শাহবাগ/শাপলার ফাঁকিটা আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।
তাছাড়া বাম-ডান, সেক্যুলার-ইসলামিস্ট উভয়-পক্ষেই অনুতাপ ও আত্মসমালোচনার অভাব বেশ প্রকট। বাঙলাদেশের বাম ও সেক্যুলারদের বৃহত্তর অংশই ইসলামপন্থীদের উপর আওয়ামী লীগের নিপীড়নের আইডিওলজিকাল জাস্টিফিকেশান তৈরী করেছে সময়ে সময়ে। পুলিশের গুলি আর ক্রসফায়ারের শব্দ না শুনে আমরা তাদের তৈরী ধর্মনিরপেক্ষতা আর অসাম্প্রদায়িকতার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকই শুনেছি বেশি। এরপরও তাদের কোনো অনুতাপ নেই, আওয়ামী লীগের কালচারাল পলিটিক্সের ছায়াতলেই কোনোরকমে নিঃশ্বাস নিয়েই এখনো তারা নিজেদের ধন্য মনে করছে। অন্য দিকে, লাগাতার নিপীড়নের শিকার হওয়া ইসলামিস্টদের একাংশও যে একটা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবেই কাজ করেছে, এইটাও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং আওয়ামী লীগের এক নিঃশ্বাসে ‘বিএনপি-জামাত’ উচ্চারণ করার মতোই আজ ইসলামিস্টরা ‘আওয়ামী-বাম’ নামক ঢালাও ন্যারেটিভ তৈরী করলে সেটা অসততার পর্যায়েই পড়বে। বিএনপি আর জামাত যেমন দুইটা ভিন্ন রাজনৈতিক সত্তা, তেমনি আওয়ামী লীগের বাইরেও বামের অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্ব যতো ক্ষীণই হোক, তাকে জায়গা দিতে হবে।
পরিশেষে
আমাদের দায়িত্ব অনেক। যে গণবিরোধী ক্ষমতা রাষ্ট্র-কাঠামোতে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, খোদ সেই ক্ষমতাকে ভেঙে দিয়েই নতুন, জনবান্ধব রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে হবে আমাদের। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের কালচারাল পলিটিক্স এবং এর যাবতীয় মিথ ও মিথ্যাগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে নিরন্তর আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে। একটা কথা মনে রাখা জরুরি। ক্ষমতা থেকে অনেকেই সরে দাঁড়ায়, কিন্তু ক্ষমতা নিজে কখনো সরে দাঁড়ায় না। গণবিরোধী ক্ষমতাকে আমরা কতোটুকু প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতাড়িত করতে পারছি, তার উপরেই নির্ভর করছে জুলাইয়ের আন্দোলনের চূড়ান্ত সার্থকতা।
তথ্যসূত্র:
১. SCHMITT, Carl (1998): Strong state and sound economy: an address to business leaders. In: CRISTI, Renato, Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism. Strong State, Free Economy, Cardiff, University of Wales Press.
২. গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন (২০১৩): বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা, রাষ্ট্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা